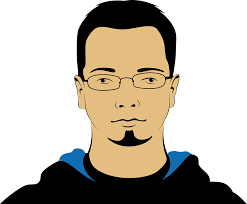
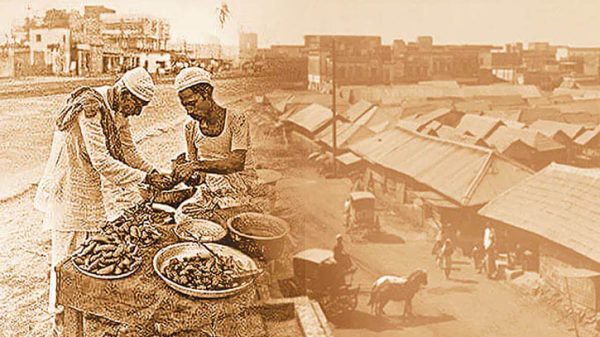

পবিত্র ঈদুল আজহা, যা আমরা কোরবানির ঈদ নামেই চিনি, অধিকাংশ মানুষ এটিকে ‘বকরি ঈদ’ বলে ডাকে। কারণ, এদিন তারা বকরি বা খাসি কোরবানি দেয়। যদিও এখন খাসির চেয়ে গরুই বেশি কোরবানি দেওয়া হয়, তবুও বাংলার মানুষের মুখে মুখে এর নাম রয়ে গেছে বকরি ঈদ।
আমার দাদা, আক্কাস মোল্লা, আমাদের পাড়া বা মহল্লার জামে মসজিদের খতিব এবং ঈদগাহের ইমাম ছিলেন। তিনি বলতেন, “কোরবানি দিতে হয় প্রিয় জিনিস। হাট থেকে একটা পশু কিনেই জবাই দিলে, সেটা অল্প সময়ে প্রিয় হয়ে ওঠে না।” তার এই কথাগুলোই যেন আমাদের কোরবানির প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দিত। তখন মানুষের গোয়াল ঘরে গরুর অভাব ছিল না। ঈদুল আজহার নামাজ শেষে কোরবানির পর, আগামী বছর কোন গরুটি কোরবানি দেওয়া হবে, তার নিয়ত তখনই করা হতো। তাই এক বছর ধরে অত্যন্ত আদর-যত্নে লালন-পালন করে সবাই কোরবানি দিতেন। সে সময় ভাগে কোরবানি দেওয়ার তেমন কোনো রীতি ছিল না, যদিও পারিবারিক অবস্থার ওপর এটি নির্ভর করত।
গরুর হাটের স্মৃতি ও প্রস্তুতি
আমার যতটুকু মনে পড়ে, আমার বাপ-চাচারা সাতজনে মিলে ৭০০ টাকা দিয়ে একটি গরু কোরবানি দিয়েছিলেন। তখন আমাদের গ্রামে গরু কেনার কোনো বাজার ছিল না। বুধবারে কংশনগর বাজার, মঙ্গলবারে মাশিকারা বাজার অথবা সোমবারে মোহনপুর বাজার থেকে গরু কিনতাম।
দূর থেকে গরু আনার জন্য কোনো পিকআপের ব্যবস্থা ছিল না। গরুর সাথে হেঁটে হেঁটে আসতে হতো, তাই দূরবর্তী কোনো বাজার থেকে গরু কিনলে আমরা ছোটরা সেখানে যেতাম না। তাছাড়া গরুর বাজার মানেই ছিল এক ভয়ের বাজার! কখন কোন্ পাগলা গরু পেছন থেকে শিং দিয়ে গুঁতো মারে, সেই ভয়ে সব সময় টেনশনে থাকতাম। তাই দূরবর্তী কোনো গাছের আগায় উঠে বাজারের সবচেয়ে বড় গরুটিকে এক নজর দেখে নিতাম। মোহনপুর বা দিঘিরপাড় বাজারে গেলে একটি বিশেষ সুবিধা ছিল; সেখানকার উচ্চ বিদ্যালয়টি ছিল দ্বিতলবিশিষ্ট। তাই দোতলার ছাদে উঠে বাজার পরিদর্শনের কাজটি সমাপ্ত করতাম। আমার সবসময়ের সঙ্গী ছিল বড় ভাই মনির, যিনি বর্তমানে ভগবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক।
গরু কেনার পর সবাই মিলে সেটিকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতাম। যে দিক থেকে গরুটি বাজারে এসেছে, সে দিকে নিয়ে যেতে কোনো কষ্ট হতো না, কিন্তু উল্টো দিকে গেলেই সমস্যা হতো। তাই আমরা আগে থেকেই গরু তাড়ানোর লাঠি সাথে নিয়ে রাখতাম। তখন মুরুব্বিরা বলতেন, “এই গরুটিকে সেবা করলে, অর্থাৎ যে যত বেশি খাওয়াতে পারবে, সে তত বেশি সওয়াব পাবে।” ফলে আমাদের বিকেল বেলার ফুটবল খেলার রুটিন পাল্টে যেত।
গরুর দাঁত ও লালন-পালন
গরু কেনার পর বাড়িতে আসার সাথে সাথেই আম্মা জিজ্ঞেস করতেন, “গরুটা কয়টা দাঁত রে মমিন?” গরু কেনার সাথে দাঁতের কী সম্পর্ক, তখনো বুঝতে পারিনি। মা আবার প্রশ্ন করলেন, “তোরা গরুর দাঁত দেখে কিনে আনিসনি?” ব্যাপারটি পরিষ্কার করলেন সালাম কাকা। তিনি বললেন, দুই বছর বয়সের নিচে গরু কোরবানি দেওয়া যায় না। বিক্রেতাগণ সত্য কথা বললে কোনো সমস্যা ছিল না। কেউ যদি কোরবানি দেওয়ার জন্য গরু কিনতে যায়, তখন হয়তো বিক্রেতা বলল, “স্যার, গরুডা গিরস্তের ঘরেই ছিল দেড় বছর, আর আমি পালছি ছয় মাস। অহন আপনিই বয়সটা হিসাব করেন।” কিন্তু আরেকজন যদি গরু মোটাতাজা করার জন্য কিনতে যায়, তাহলে সে হয়তো বলল, “গরুর বয়স মাত্র এক বছর। উন্নত জাতের গরু তো, তাই একটু মোটা-তাজা দেখা যায়। আসলে একেবারে কচি গরু।” গরুর দুধ দাঁত পড়ে নতুন দাঁত উঠতে সময় লাগে দুই বছর। তাই দাঁত দেখে গরু কিনলে আর কোনো সন্দেহ থাকত না। এভাবেই সালাম কাকা আমাকে বুঝিয়েছিলেন। এছাড়া শিংয়ের মধ্যকার গোল দাগ দেখেও বয়স অনুমান করা যেত।
তখন সকল গিরস্তের গরু রাখার ঘর ছিল। তাই সবাই একদিন একদিন পরে পালাক্রমে কোরবানির গরুটিকে নিয়ে রাখত। তবে যার ঘরেই গরু থাকুক না কেন, আমরা ছোটরা সবসময় সেই গরুর জন্য কচি ঘাস, ভাতের মাড় ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতাম। তখন গরু মোটাতাজাকরণের কোনো মেডিসিন ছিল না। আমরা ধান থেকে প্রাপ্ত কুঁড়া, সরিষা থেকে খৈল, গুড় থেকে প্রাপ্ত রাব খাইয়ে গরুর যত্ন নিতাম।
প্রতিযোগিতামূলক কোরবানি ও বড় গরু দেখার উন্মাদনা
কে কত বড় কোরবানি দিতে পারে, সে প্রতিযোগিতা তখনও কম-বেশি ছিল। ঈদের ১৫ দিন আগে আমরা গ্রামের অলি-গলি ঘুরে দেখা শুরু করতাম কে কত বড় গরু এনেছে এবং কোন গরুর রঙ কীরকম। কোনটি বেশি দুষ্ট, তা আমাদের নখদর্পণে থাকত।
একবার আমাদের বাড়ির উত্তর দিকের মুন্সি বাড়িতে আঠারো হাজার টাকা দিয়ে কালো রঙের একটি ষাঁড় গরু কেনা হয়েছিল। সে কী বিশাল গরু! আমরা ভয়ে তার কাছে যেতাম না, দূর থেকে গাছের পাতা ছুড়ে মারতাম। সেটি খেয়ে গরুটি আমাদের দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকত, মনে হতো সে যেন আল্লাহর কাছে দোয়া করছে। বিশাল গরুটি দেখার জন্য কয়েক গ্রামের লোক এসে ভিড় করেছিল।
আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ আসে ১৯৮৩ সালে। তবে সে সময় গ্রামের কারো ঘরে ফ্রিজ ছিল না। তাই বড় গরু কিনে তা ফ্রিজে রাখার রেওয়াজ তখনও চালু হয়নি। যারা বড় গরু কোরবানি দিতেন, তারা অতিরিক্ত মাংস গরিব-মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তখন শুনতাম, তিনদিনের বেশি কোরবানির গোশত জমা করে রাখা যায় না।
আমাদের গ্রামে ছিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের বাড়ি। তিনি কুঁড়েঘর মার্কা নিয়ে রাজনীতি করতেন। লাল রঙের একটি বিশাল বড় গরু মোজাফফরের মাঠে বাঁধা বাঁশের খুঁটিতে আটকে রাখতে দেখতাম। কোরবানির পরদিন সকালে লাল টুপি মাথায় দিয়ে ন্যাপের কর্মীরা সেটি কোরবানি করে গরিব নেতাকর্মীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।
কোরবানির পর: ঢোল বাজানো ও শিংয়ের ব্যবহার
নামাজ শেষে দ্রুত বাড়ি আসতাম। কার গরু কখন জবাই হয়, সেই খবর নিয়ে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখতাম। কোনটি স্বাভাবিকভাবে আমার দাদা জবাই করলেন, আর কোনটি জবাইয়ের সময় উঠে দৌড় দিল, তারপর আবার সবাই রক্তমাখা গরুটিকে ধরে এনে পুনরায় শুইয়ে দিল, তা খেয়াল রাখতাম।
অন্যদের গরু জবাইয়ের দৃশ্য দেখা শেষ হওয়ার পর হঠাৎ মনে হতো ঢোল বানানোর কথা। আর তো ঘুরাঘুরি করা যায় না! দৌড়ে আসতাম আমাদের গরুর কাছে। এতক্ষণে গরুর কাজ অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে। অপেক্ষায় থাকতাম কখন গরুর পেট থেকে বের করা হবে চর্বি জাতীয় এক ধরনের সাদা পর্দা। বড় ভাই সেগুলো আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। আমরা সেগুলো ভাঙা কলসের মুখে লাগিয়ে টিনের চালে শুকাতে দিতাম। কলসের খুলি ঈদের চার-পাঁচ দিন আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখতাম। বিকেল হলেই কচুর চিকন ডগা দিয়ে বাজানো শুরু করতাম ঢোল। ডুম-ডুম আওয়াজে মাতিয়ে তুলতাম সব বাড়ি। একসময় কারটা কত বেশি বাজানো যায়, সে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে সেটি ফেটে গেলে কান্নাকাটি করতাম।
বাড়িতে যাতে প্রেতাত্মা না ঢোকে, সেজন্য গরুর শিংগুলো দরজার পাশে ঝুলিয়ে রাখতাম। লাউ ক্ষেতে যাতে কারো নজর না লাগে, সেজন্য গরুর দু’পাটি দাঁত লাউয়ের মাচার নিচে ঝুলিয়ে রাখতাম। মধুর আনন্দঘন সেই দিনগুলো ঢোলের আওয়াজের মতো হারিয়ে গেছে জীবন থেকে। খুব মিস করি সেই দিনগুলোকে। খু—উ—ব। খুব বেশি।
লেখক পরিচিতি: সাংবাদিক, ঐতিহ্য গবেষক ও মুরাদনগরের সামছুল হক কলেজের সিনিয়র প্রভাষক, মমিনুল ইসলাম মোল্লা।